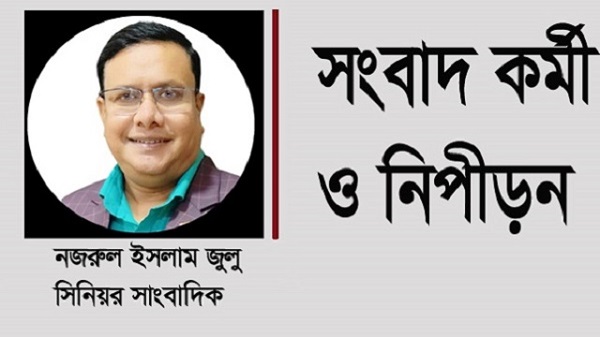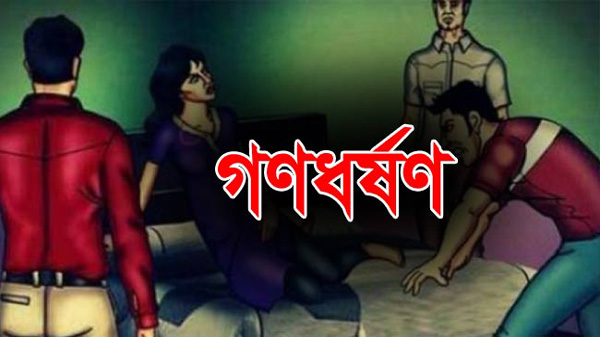অর্থের সঙ্গে মিলছে না সমাজের তাল
- প্রকাশের সময় : মঙ্গলবার, ২৩ জানুয়ারী, ২০১৮
মাসুদা ভাট্টি: দেশের অর্থনীতির গতির সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির সম্পর্ক থাকছে না বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, যদিও এ বিষয়ে গবেষণার কোনো তাগিদ দেখা যাচ্ছে না একাডেমিকদের মধ্যে। এদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত: গবেষণা করে সেসব বিষয় নিয়ে যেসব ফলাফল নিয়ে রাজনীতি করা যায়, সরকারকে এক হাত নেয়া যায়। তাও আবার বিশেষ সরকারের আমলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি যেনো খেপে ওঠে তাদের রাজনৈতিক গবেষণা নিয়ে। এমনও দেখা যায় যে, তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা না দিয়েই এমন এক গবেষণা-ফলাফল প্রকাশ করে যে মনে হতেই পারে এর পেছনে বড় ধরনের কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে।
সেদিক দিয়ে এদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিও এক ধরনের রাজনীতিই করে, বিদেশি অর্থায়নে কিংবা নিজস্ব অর্থায়নে তারা উদ্দেশ্যপ্রবণ হয়ে ওঠে নিজেদের রাজনীতির পক্ষে যাওয়ার মতো বিষয়কে গবেষণার বিষয় নির্বাচন করে। নামোল্লেখ না করে অতি সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি গবেষণা-ফলাফল যা এদেশের গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে (এক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব ও পছন্দের গণমাধ্যমও রয়েছে, যেখানে তারা চাইলেই তাদের গবেষণা-ফলাফল প্রকাশ ও প্রচার করতে পারে এবং করেও থাকে) সেগুলোর উদাহরণ টানতে পারি কিন্তু আজকের লেখার বিষয় তা নয়, আজকে এদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির পার্থক্য নিয়েই কথা বলতে চাইছি।
প্রায়শঃই বলে থাকি যে, ওই সমাজে কোনো প্রাণ নেই, মানুষে মানুষে সম্পর্ক নেই। হতে পারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ সেখানে প্রবল, ফলে একজন মানুষের পরিচিতির গণ্ডির মতো সমাজে তার অবস্থান নিয়ে তারা খুব বেশি চিন্তিত নয়। কিন্তু বাংলাদেশে থেকে আমরা যার সমালোচনা করি সেই একই দিকে যদি আমরাও এগুতে থাকি তাহলে আর সমালোচনার সুযোগ থাকে কি?
অর্থনৈতিক ভাবে দেশ কতোটা এগিয়ে গেছে তা জানার জন্য আমাদের খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না গুগুল সার্চ দিলেই অনেক তথ্য বেরিয়ে আসে যেমন, মানুষের গড় আয় কতো বাড়লো, সরকারের ব্যাংকঋণের পরিমাণ কতো কিংবা দেশের প্রবৃদ্ধি কতো শতাংশ ইত্যাদি। কিন্তু কোনো দেশের সামজিক উন্নয়নের সূচক খুব সহজে পাওয়া যায় না, এর জন্য প্রয়োজন পড়ে বিশেষ গবেষণার। আগেই বলেছি যে, সে বিষয়ে গবেষণার আগ্রহ খুউব কম এদেশে।
এতোদিন বেশ কিছু বেসরকারি সংস্থা সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে এদেশে কাজ করেছে কিন্তু যখন থেকে এদেশে ক্ষুদ্রঋণের ব্যবসা শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই এই সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে কাজ করা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি এই ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ-ব্যবসায় মনোনিবেশ করেছে, ফলে দেশের সামাজিক অগ্রগতি নিয়ে মূলত: এখন সরকারই কাজ করছে। এর বাইরে যারা এ নিয়ে আগ্রহী তাদের বিদেশি সাহায্যও কমে গেছে বলে অভিযোগ শুনেছি।
কিছুদিন আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাসউদ্দিন এক লেখায় দেশের সামাজিক অগ্রগতি বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য উল্লেখ করেছেন যা গবেষকদের কাজে আসতে পারে। তিনি মূলত: শিক্ষাখাত, গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতি, শিশুমৃত্যু-মাতৃমৃত্যুর হার কমানো, নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার ইত্যাদি কিছু সূচকে অগ্রগতি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেছেন। তার সঙ্গে দ্বিমতের সুযোগ কম, নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনও বাংলাদেশের এসব অগ্রগতিতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই দুই অর্থনীতিবিদ যে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেননি তাহলো সাধারণ মানুষ কি দেশের এই অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের সামাজিক অবস্থানকে মিলিয়ে সে অনুযায়ী মানিয়ে চলতে পারছে? পারছে কি দেশের এই অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতর এনে একটি শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে? আমি নিশ্চিত দুই অর্থনীতিবিদের কাছেই এ বিষয়ে সম্মক কোনো ডাটা বা তথ্য/উপাত্ত নেই। এই মুহূর্তে আমিও যে লেখাটি লিখছি এ বিষয়ে, আমার হাতেও গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যাদি ছাড়া উল্লেখ করার মতো কোনো তথ্য নেই।
সমাজকে অস্থিতিশীল করে দারিদ্র্য- অর্থনীতির পণ্ডিতরা এ বিষয়ে বিস্তর লিখেছেন। বাংলাদেশও যখন দরিদ্র ছিল (এখনও যে সম্পূর্ণ দারিদ্র্যমুক্ত হয়েছে সে দাবি করছিনে) তখন এদেশের সামাজিক অবস্থা এতোটা অস্থিতিশীল ছিল কিনা সে বিষয়েও কোনো তুলনামূলক তথ্য হাজির করতে পারছিনে। কিন্তু একথা বলতেই পারি যে, সাদা চোখে এদেশে সামাজিক অস্থিরতা বিশেষ করে হত্যাকাণ্ড, দুর্নীতি, তৃণমূল পর্যায়ে সংঘর্ষ ইত্যাদি আজকের মতো এতোটা লাগামহীন ছিল কি?
প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, তখন গণমাধ্যমের এতো উন্নতি হয়নি ফলে সেসময়কার তথ্যাদি বিষয়ে হলপ করে কিছুই বলা যায় না। এই অজুহাত মেনে নিয়েও আজকের যে সমাজে আমরা বসবাস করছি তা যেনো মায়া-দয়াহীন নিষ্ঠুর এক সমাজ, যেখানে মানুষে মানুষের সম্পর্ক আল্গা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ:, স্বার্থপরতা, নীচুতা, হত্যা-ধর্ষণ-নির্যাতন ও ক্ষমতার বাড়াবাড়ি এতোটাই বেড়েছে যে, একে সমাজ স্বাভাবিক বলেই মেনে নিচ্ছে বা এর বিরুদ্ধে কোনো সংঘবদ্ধ প্রচার-প্রচারণা বা প্রতিবাদ নজরে আসছে না।
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলি তাদের ভূমিকা বদলের চেষ্টা করছে, অর্থনৈতিক অগ্রগতি রাষ্ট্রকে সেই অবস্থানে ক্রমশ: নিয়ে আসছে যেখান থেকে নাগরিকের জানমালের নিরাপত্তা প্রদানে যেনো এই সংস্থাগুলো প্রয়োজনীয় সেবা দিতে পারে। সর্বক্ষেত্রে তার প্রয়োগ হচ্ছে সে দাবি করার উপায় নেই, তবে অনেক অপ-উদাহরণের মাঝেও ভালো কাজের নমুনা ইদানিং বেড়েছে। ৯৯৯ নাম্বারে ফোন করে প্রাথমিক সাহায্য চাওয়ার যে সুযোগ এখন তৈরি হয়েছে ধরেই নিচ্ছি অতি দ্রুত এই সেবাকার্য জনগণের জন্য একটি ভরসার জায়গা হয়ে উঠবে। কিন্তু নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে কবে কোন্ দেশ সর্বোতভাবে সমাজকে শুদ্ধ করতে পেরেছে? খুব বেশি উদাহরণ এক্ষেত্রে আমাদের সামনে নেই।
অনেকেই বলে থাকেন যে, সমাজে অন্যায়-অনাচার তখনই বেড়ে যায় যখন মানুষ ধর্মচ্যুত হয়। বাংলাদেশকে আর যে কোনো দোষেই দোষী করা যাক না কেন, এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মচ্যুত হয়েছে সে দোষ দেওয়া যাবে না। গত ৪০ বছরে এদেশে সবচেয়ে যে প্রপঞ্চটি মানুষকে ও সমাজকে দখলে রেখেছে তাহলো ধর্ম। তবে এক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ ‘লালসালু’ উপন্যাসের সেই অমোঘ বাক্যটি স্মরণযোগ্য, “যে দেশে শস্যের চেয়ে টুপি বেশি”- আমি নিশ্চিত ভাবেই একে সত্য বলে ধরে নিতে চাইনে কিন্তু একে অস্বীকার করার মতো সাহসও নেই।
কিন্তু কেবলমাত্র ধর্ম দিয়েই কোনো সমাজকে অনাচারমুক্ত রাখা সম্ভব হলে কট্টর ধর্মবাদী দেশগুলিতে সমাজে কোনো ধরনের অন্যায়-অনাচার থাকতো না, যেমন আমরা সৌদি আরবের কথা বলতে পারি। কিংবা যে সব দেশে সেই অর্থে ধর্মাচরণ তেমন নেই বললেই চলে সেসব দেশ সামাজিক অনাচারের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হতো, উদাহরণ হিসেবে ইউরোপের দেশগুলির কথা বলা যায়। না সৌদি আরবের সমাজ একটি আদর্শ সমাজ, না ইউরোপের সমাজ একটি ভয়ঙ্কর অনাচারী সমাজ, দু’টোর কোনোটিই সত্য নয়। অর্থাৎ ধর্ম সমাজ বিনির্মাণে সামান্য ভূমিকাই রাখতে পারে।
এক্ষেত্রে শিক্ষা নিশ্চিতভাবেই একটি প্রপঞ্চ হতে পারে, আমরা যেসব দেশকে উন্নত সমাজ ব্যবস্থার দেশ হিসেবে চিহ্নিত করি, সেসব দেশ শিক্ষাকে সমাজ বিনির্মাণে কিংবা বদলে একটি ‘টুল’ হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে যাওয়া অনেক শিশু-কিশোরকেই প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি যে, এসব দেশে শিক্ষা গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের সমাজের অনেক কিছুর সঙ্গেই তারা আর নিজেদের মেলাতে পারে না। স্কুলের শিক্ষা থেকেই তাদের মিথ্যে না বলার অভ্যেস তৈরি হয়। সমাজে তাদের অংশগ্রহণ, অবস্থান কিংবা ভ’মিকা বিষয়ে তারা শিশুকাল থেকেই একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষা নিয়ে বেড়ে ওঠে। অনেকেই আমরা পশ্চিমা সমাজব্যবস্থার আবেগহীনতা ও অতি-বাস্তব এবং কঠোরতা নিয়ে সমালোচনা করি।
প্রায়শঃই বলে থাকি যে, ওই সমাজে কোনো প্রাণ নেই, মানুষে মানুষে সম্পর্ক নেই। হতে পারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ সেখানে প্রবল, ফলে একজন মানুষের পরিচিতির গণ্ডির মতো সমাজে তার অবস্থান নিয়ে তারা খুব বেশি চিন্তিত নয়। কিন্তু বাংলাদেশে থেকে আমরা যার সমালোচনা করি সেই একই দিকে যদি আমরাও এগুতে থাকি তাহলে আর সমালোচনার সুযোগ থাকে কি? রাস্তায় ফেলে এক ব্যক্তি একজন নারীকে বেধড়ক পেটাচ্ছে আর আশেপাশের মানুষ সেটা দেখছে কিংবা মোবাইল বের করে ভিডিওচিত্র ধারণ করছে, এটা এই সমাজের এই মুহূর্তের বাস্তবতা।
স্কুলছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করছে একদল ছেলে আর পথচলতি কোনো মানুষ তার প্রতিবাদটুকু করছে না কিংবা ক্লাশ সেভেনের ছেলেকে তারই বন্ধুদল মিলে হত্যা করছে- একটি সমাজে যখন এরকম ভয়ঙ্কর অস্থিরতার সুযোগ তৈরি হয় তখন সেই সমাজ যতোই অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে যাক না কেন, তা আসলে এক সময় ভেঙে পড়তে বাধ্য। এর জন্য এদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাকে আমরা দায়ী করতেই পারি কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ সত্য প্রতিফলিত হয় না, হওয়ার কথা নয়। এর পেছনে আরো অনেকগুলো কারণ আছে, যেগুলো অতি দ্রুত আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুফল ভোগ করবো আর সামাজিক অগ্রগতিকে থামিয়ে রাখবো সেটা হয় না, হতে পারে না। দুই অগ্রগতির সমন্বয় সাধন প্রয়োজন এবং সেটা অবিলম্বেই।
খবর২৪ঘণ্টা.কম/রখ
এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার সম্পুর্ণ বেআইনি।